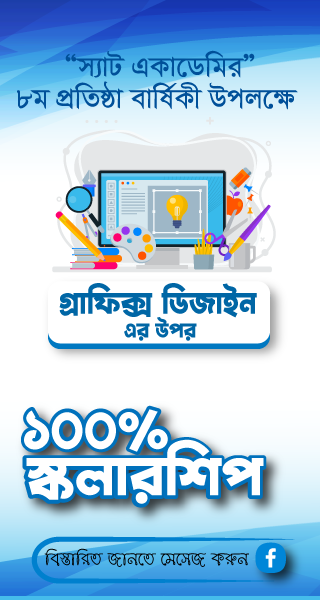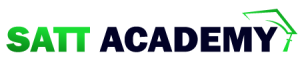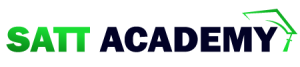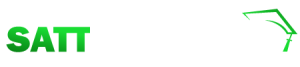কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে এর মধ্যদিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। পরিবাহীর মধ্যদিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির কিছু অংশ পরিবাহীর রোধ অতিক্রম করার কাজে ব্যয়িত হয়। এই ব্যয়িত শক্তি পরিবাহীতে তাপ শক্তিরূপে প্রকাশ পায় এবং এর ফলে পরিবাহী উত্তপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়া বলা হয় । আমরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ তড়িৎ প্রবাহের এই তাপীয় ক্রিয়াকে কাজে লাগাই । বৈদ্যুতিক হিটার বা চুলা, কেতলি, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক বাতি, ফিউজ, ফার্নেস প্রভৃতি সবই তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়ার ব্যবহারিক রূপ। বিজ্ঞানী জেম্স প্রেসকট জুল তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়া আবিষ্কার করেন বলে একে জুলের তাপীয় ক্রিয়াও বলা হয় ।
তড়িৎ প্রবাহের ফলে তড়িৎ বর্তনীতে যে তাপের উদ্ভব হয় তার কারণ ইলেকট্রন মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তড়িৎ পরিবাহীতে বেশ কিছু সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। পরিবাহীর দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো আন্তঃআণবিক স্থানের মধ্যদিয়ে পরিবাহীর নিম্ন বিভব বিশিষ্ট বিন্দু থেকে উচ্চ বিভববিশিষ্ট বিন্দুর দিকে চলতে থাকে, ফলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই ইলেকট্রনগুলো চলার সময় পরিবাহীর পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ইলেকট্রনের গতিশক্তি পরমাণুতে সঞ্চালিত হয় এবং পরমাণুর গতিশক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয় এবং পরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ জন্য তড়িৎ প্রবাহের ফলে বর্তনীতে তাপের উদ্ভব পমাত্রা বৃদ্ধি পায় । এ জন্য তড়িৎ প্রবাহের ফলে বর্তনীতে তাপের উদ্ভব হয়।
জুলের তাপীয় ক্রিয়ার সূত্র (Joule's Laws for Heating Effect)
পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ এবং প্রবাহের সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য জুল সর্বপ্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং এ সম্পর্কে তিনটি সূত্র উপস্থাপন করেন। এগুলোকে জুলের সূত্র বলা হয়।
প্রথম সূত্র-তড়িৎ প্রবাহের সূত্র : পরিবাহীর রোধ (R) এবং প্রবাহকাল (t) অপরিবর্তিত থাকলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত তাপ (H) প্রবাহের (l) বর্গের সমানুপাতিক হয়।
এ সূত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীতে নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো প্রবাহ চালালে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার দ্বিগুণ প্রবাহ সমান সময় ধরে চালালে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ চার গুণ হবে, প্রবাহ তিন গুণ করলে তাপের পরিমাণ নয় গুণ হবে।
কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে l1,l2,l3 .................... প্রবাহ সমান সময় ধরে চালালে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ যথাক্রমে, H1,H2,H3……. হলে, এই সূত্রানুসারে,
দ্বিতীয় সূত্র রোধের সূত্র : প্রবাহ (I) এবং প্রবাহকাল (t) অপরিবর্তিত থাকলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত তাপ (H) পরিবাহীর রোধের (R) সমানুপাতিক হয় ।
অর্থাৎ H R, যখন l ও t ধ্রুব।
এই সূত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোধের পরিবাহীর ভেতর দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ একই সময় ধরে চালালে, রোধ দ্বিগুণ হলে উদ্ভূত তাপ দ্বিগুণ হবে, রোধ অর্ধেক হলে উদ্ভূত তাপ অর্ধেক হবে ।
একই পরিমাণ প্রবাহ একই সময় ধরে R1,R2,R3….রোধের ভেতর দিয়ে চালালে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ যথাক্রমে H1,H2,H3….হলে, এই সূত্রানুসারে,
=… ধ্রুব।
তৃতীয় সূত্র-সময়ের সূত্র : প্রবাহ (I) এবং পরিবাহীর রোধ (R) অপরিবর্তিত থাকলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত তাপ (H) প্রবাহকালের (t) সমানুপাতিক হয়
অর্থাৎ H l, যখন l ও R ধ্রুব।
এই সূত্রানুসারে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর ভেতর দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ বিভিন্ন সময় ধরে চালালে, প্রবাহকাল দ্বিগুণ হলে উদ্ভূত তাপ দ্বিগুণ হবে, প্রবাহকাল অর্ধেক হলে উদ্ভূত তাপ অর্ধেক হবে।
কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর ভেতর দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ t1,t2,t3….. সময় ধরে চালালে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ যথাক্রমে H1, H2,H3……. হলে, এই সূত্রানুসারে,
= ধ্রুব।
তাপের যান্ত্রিক সমতা,
তাপের সাবেক একক : ক্যালরি
আমরা জানি, তাপ শক্তির একটি রূপ এবং তাপের একক জুল। এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অর্থাৎ এস. আই একক চালু হওয়ার আগে তাপের বিভিন্ন এককের প্রচলন ছিল, যার মধ্যে ছিল ব্রিটিশ তাপীয় একক এবং ক্যালরি (cal)। ক্যালরি এককটি বহুল প্রচলিত ছিল। বিশ্বজুড়ে এস. আই পদ্ধতি চালু হওয়ায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নেই। যদিও এখনও দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য লেখায় ক্যালরির ব্যবহার দেখা যায়।
এক গ্রাম (1g) বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস (1°C) বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপকে এক ক্যালরি (1 cal) বলে।
আমরা জানি, গৃহীত বা বর্জিত তাপ = ভর x আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য
বা, H = ms
ক্যালরি ও জুলের সম্পর্ক : তাপের যান্ত্রিক সমতা J
আমরা জানি, তাপ এক প্রকার শক্তি। অন্যান্য শক্তিকে যেমন তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তেমনি তাপশক্তিকেও অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে শক্তির একক একটিই জুল এবং তাপের এককও জুল। কিন্তু আগে যখন তাপের একটি একক হিসেবে ক্যালরি প্রচলিত ছিল তখন হিসাব নিকাশের জন্য জুলকে ক্যালরিতে বা ক্যালরিকে জ্বলে রূপান্তরের প্রয়োজন হতো। এর জন্য ক্যালরি ও জুলের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অপের যান্ত্রিক সমতা এর মাধ্যমে এ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। তখন কাজ বা যান্ত্রিক শক্তিকে 'জুল' এবং তাপশক্তিকে 'ক্যালরি' এককে পরিমাপ করা হতো। W জুল কাজ সম্পন্ন করলে যদি H ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হতো বা H ক্যালরি তাপ প্রয়োগে যদি W জুল পরিমাণ কাজ পাওয়া যেত তাহলে শক্তির নিত্যতা তথা সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা পাই,
H ক্যালরি = W জুল।
বা, I ক্যালরি = জুল।
এই অর্থাৎ কাজ ও তাপের অনুপাতকে বলা হয় তাপের যান্ত্রিক সমতা। বিজ্ঞানী জুল সর্বপ্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্থাপন করেন অর্থাৎ -এর মান নির্ণয় করেন। এজন্য এই অনুপাত অর্থাৎ তাপের যান্ত্রিক সমতাকে J দ্বারা H
প্রকাশ করা হয় ।
:- J =
এই সমীকরণ থেকে দেখা যায়
H = 1 একক হলে J = W হয় ।
তাপের যান্ত্রিক সমতা j -কে তাই নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় :
একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় বা একক তাপ দ্বারা যে পরিমাণ কাজ করা যায়, তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে।
বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে কাজ বা ব্যয়িত শক্তি W-কে জ্বলে পরিমাপ করে এবং উৎপাদিত তাপ H-কে ক্যালরিতে পরিমাপ করে (3,4) সমীকরণে মান বসিয়ে J-এর মান পাওয়া গেছে,
J = 4.2
অর্থাৎ 1 ক্যালরি তাপ দ্বারা 4.2 জুল কাজ করা যায়, বা ক্যালরি তাপ উৎপন্ন করতে 4.2 জুল কাজ করতে হয় । অর্থাৎ ক্যালরি এবং 4.2 জুল পরস্পর সমান ।
সুতরাং 1 ক্যালরি = 4.2 জুল।
যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে তড়িৎ কোষ ৰলে ।
কোনো কোনো কোষ বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। যেমন- লেকল্যান্স কোষ, শুষ্ক কোষ ইত্যাদি।
কোনো কোনো কোষ বাইরে থেকে পাঠানো তড়িৎ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে রাখে এবং পরে সেই রাসায়নিক শক্তিকে পুনরায় তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। যেমন-সীসা এসিড সঞ্চয়ক কোষ।
কোষের তড়িচ্চালক শক্তি (Electromotive Force or emf. of Cell)
তড়িচ্চালক শক্তি হয় কোনো কোষের বা কোনো তড়িৎ উৎসের। কোনো কোষের কাজ হচ্ছে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা অর্থাৎ কোষের সংযোগকারী বর্তনীর ভেতর দিয়ে আধান চালনার জন্য প্রয়োজনীয় তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করা।
তড়িচ্চালক শক্তি দ্বারা কোষের বা তড়িৎ উৎসের এই তড়িৎ শক্তির পরিমাপ পাওয়া যায়। প্রতি একক আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ঐ বিহুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কোষ যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে তাকে ঐ কোষের তড়িচ্চালক শক্তি বলে ।
q আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে পুনরায় ঐ বিন্দুতে আনতে যদি W কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে কোষের তড়িচ্চালক শক্তি,
মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ যখন তড়িৎ প্রবাহ চলে না তখন কোষের দুই পাতের যে বিভব পার্থক্য হয় তার দ্বারা কোষের তড়িচ্চালক শক্তি পরিমাপ করা হয়। যখন কোষটি তড়িৎ প্রবাহ চালনা করে তখন এর দুই পাতের বিভব পার্থক্য কোষের তড়িচ্চালক শক্তির চেয়ে কম হয়।
একক : যেহেতু, তড়িচ্চালক শক্তি হচ্ছে =কাজ/আধান তাই কাজের একককে আধানের একক দিয়ে ভাগ করলে তড়িচ্চালক শক্তির একক পাওয়া যায়। সুতরাং তড়িচ্চালক শক্তির একক হচ্ছে =জুল/কুলম্ব বা JC-1 অর্থাৎ ভোল্ট (V)।
দেখা যাচ্ছে, তড়িচ্চালক শক্তি ও বিভব পার্থক্যের একক একই অর্থাৎ ভোল্ট (V)।
একটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তি 1.5 V বলতে বোঝায় । C আধানকে ঐ কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে একবার সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে পুনরায় ঐ বিন্দুতে আনতে 1.5J কাজ সম্পন্ন হয় ।
কোনো কোষের দুই প্রান্ত একটি পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে পরিবাহীর যুক্ত ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। ইলেকট্রনগুলো যে গড় বেগে প্রবাহিত হয় তাকে সঞ্চরণ বেগ বা তাড়ন বেগ বলে। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ I হলে,
I = nAve
Promotion